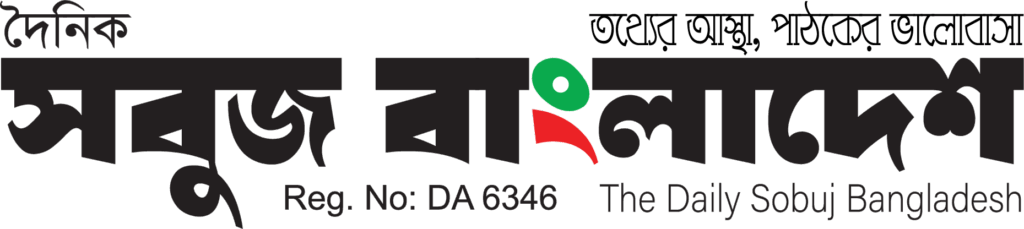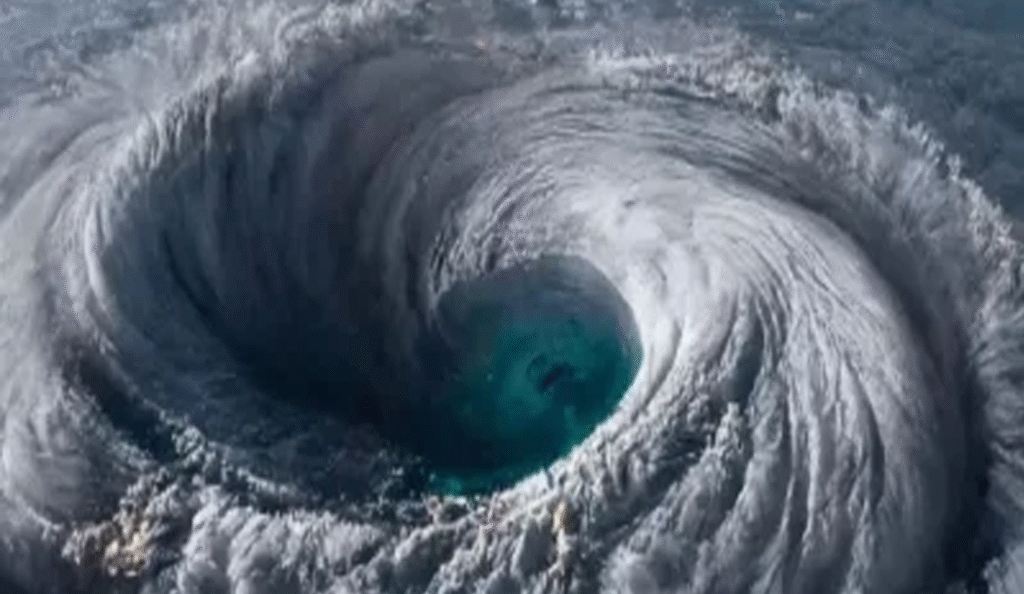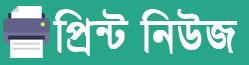
” শওকত মাহমুদ”
রাষ্ট্র সংস্কারের প্রণোদনা এবং আলোচনা এখন সর্বত্র। হাজার প্রাণের বিনিময়ে সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের লক্ষ্যও ছিল তাই। সরকার প্রথমে ছয়টি এবং পরে চারটি কমিশন গঠন করেছে। মিডিয়াসংক্রান্ত কমিশনটি হয়েছে সিনিয়র সাংবাদিক কামাল আহমেদের নেতৃত্বে। তাকে অভিনন্দন জানাই। তথ্য পরিচালকরা বলছেন, লোক নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। আশা করি শিগগিরই হয়ে যাবে এই কমিশন। কেননা, রাষ্ট্র সংস্কারের অবশ্য-অঙ্গ হতে হবে মিডিয়ার। হাসিনার দুঃশাসন সংবাদপত্র জগৎকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। হাতেগোনা দলকানা কয়েকটি সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিককে ধনী বানানোর বিনিময়ে ব্যাপক সাংবাদিক সমাজকে আর্থিকভাবে পঙ্গু, মানসিকভাবে পর্যুদস্ত এবং সত্য বলার অধিকার থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনেকেই আছেন সম্ভাব্য সংস্কারকে তাচ্ছিল্যভরে দেখছেন। প্রতিবিপ্লবের আশায় আছেন। ভাবখানা হচ্ছে ওসব করে কী হবে? দরকার নেই। ওই যে এক মরমি কবি বলেছেন, ‘মাটির জনম না ছিল যখন তখনও করেছি চাব, দিন রজনী না ছিল যখন তখনও গনেছি মাস।’ আমরা অমন নকলি নবাবের জাতি। প্রথমেই বলে রাখি, এই কমিশনের নাম হওয়া উচিত ‘বাংলাদেশ প্রেস কমিশন’। ‘মিডিয়া কমিশন’ নয়। প্রেস শব্দটার ব্যাপ্তি বেশি এবং এটা মুদ্রিত, বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক এবং অন্য যে কোনো তথ্যমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে। সংবিধান প্রণেতারা ‘প্রেস’ এবং বাংলা করেছেন ‘সংবাদ ক্ষেত্র’। মিডিয়া শব্দটির চল বেশি দিনের নয়, টিভি-রেডিওর সাংবাদিকতা থেকে উৎসারিত। সংবিধান ও আইনের সংস্কার হাসিনা সরকারের বিতর্কিত পঞ্চম সংশোধনী প্রথমবারের মতো সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর খড়গ এনেছে, তা লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। ৭ ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বলা হয়েছে, ‘কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে। কোন ব্যক্তি উপর্যুক্ত কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে তাহার এই রূপ কার্যও অপরাধ হইবে।’ বুঝলাম, ক্যু ঠেকাতে এই অনুচ্ছেদ। এটা সংবিধান সংস্কার কমিশন বুঝবে কী হবে এর পরিণতি। এখন তো সংসদ ভাঙার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে না। এর আইনি বিহিত কি হবে? ইমার্জেন্সি দিয়ে ২০০৭ এর ২২ জানুয়ারি নির্বাচন আটকে দেওয়া হয়েছিল। এবার কী হবে? এই মাথাব্যথা বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকদের। কিন্তু আমার চিন্তা হলো ‘মতপ্রকাশ’কে যদি ‘ষড়যন্ত্র’ গণ্য হয় এবং এই সংবিধানের যে কোনো বিধানের প্রতি আস্থা পরাহত করার চেষ্টা বা মতপ্রকাশকে যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতা বিবেচনা করা হয়, তাহলে আমি যাব কোথায়? সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ বা দফা সম্পর্কে সমালোচনা করার অধিকার নাগরিকরা হারিয়ে ফেলেছে। অতএব এর সংশোধন জরুরি। দ্বিতীয়ত ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, “চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।” এই অনুচ্ছেদটির সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের কিংবা বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের এমনকি সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ বা ইউরোপীয় কনভেনশনের কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু গোলমালটা হচ্ছে, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কবিষয়ক শর্তের ক্ষেত্রে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম আলোচিত রাজনীতিবিদ মরহুম আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রেস কমিশন হয়েছিল। শীর্ষ সম্পাদকরা ছিলেন এর সদস্য। এই কমিশনের রিপোর্ট বলছে, “বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার শর্তটি ভারত বাদে বিশ্বের আর কোন সংবিধানে পাওয়া যায় না। ভারতের সংবিধানে এটা ঢুকেছে ১৯৫১ সালের প্রথম সংবিধান সংশোধন আইনে। … এই শর্তটির ক্ষেত্রে অনেকেই আপত্তি দিয়েছেন এই বলে যে, সংবাদপত্রের দায়িত্ব হচ্ছে বৈদেশিক সম্পর্ককে পর্যালোচনা করা। এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, পত্রিকার রিপোর্টের জন্য কোন বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। কমিশন মনে করে, ‘We are also of the viwe that the press should be free to express opinion and analyse development on relations with foreign states. There can be no deûing the fact that such discussion serve a useful purpose by presenting points of viwe which otherwise would not have been known. It should also be appreciated that foreign policy and relations with foreign states are not static and healthy discussion in the press would rather he helpful in effecting the desired changes.’ প্রেস কমিশনের এই সুপারিশ কেউ কানে তোলেনি। বরং ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার অপরাধ আইনে এ সংক্রান্ত ধারা জুড়ে দিয়ে সাংবাদিকদের সন্ত্রস্ত করেছে। দুর্জনের মতে, ভারত বিরোধিতা রুখতে এই বিধান। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত বাক, ব্যক্তি, চিন্তা, বিবেক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সামান্যই আইন আছে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞামূলক বা সাবধানী আইন বেশি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক জনাব মতিন বলেছেন, ওই নিশ্চয়তা দানমূলক দফা দিয়ে যুক্তিসংগত বাধার দফাগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায়। এর ক্ষমতার তুলনা তিনি করেছিলেন হজরত মুসা (আ.)-এর জাদুকরী লাঠির সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমাদের বিচার বিভাগ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে যুগান্তরী রায় দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। ‘আমার দেশ’-এর মজলুম সম্পাদক মাহমুদুর রহমান উচ্চ আদালত সম্পর্কে লেখালেখির জন্য জেল খেটেছেন। তিনি আদালতের কাছে ক্ষমা চাননি। এক বিচারপতি ওই শুনানির সময় এমন মন্তব্যও করেছেন যে, Truth is no defense (সত্য কোনো রক্ষাকবচ নয়)। অথচ ভারতীয় সংবিধানে ‘Press freedom’ শব্দ দুটি না থাকলেও উচ্চ আদালতগুলো নানা রায়ে মৌলিক ও মানবাধিকারের উল্লেখ করে মতপ্রকাশের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আইন-সংস্কার বাংলাদেশে প্রচলিত নানা আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে নানা কিসিমের গিঁট্টু থাকে। সম্ভাব্য কমিশনকে অবশ্যই দেখতে হবে সাইবার অপরাধ আইন, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ সালের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন, আদালত অবমাননা আইন, সচিবালয় নির্দেশিকা ইত্যাদি আইনগুলো। তথ্য অধিকার আইনে তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। আচ্ছা, সংবাদপত্র বা টিভির লাইসেন্সিং প্রথা তুলে দেওয়া যায় না? এসবের নামে হয়রানি এবং অপমানজনক মুচলেকা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। কদিন আগে মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক সাংবাদিক জিমি আমির এক আলোচনা সভায় বলছিলেন, ‘সংবাদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন আলাদা রেখে মূল কার্যক্রম পরিচালনা করা। অর্থাৎ যেসব মালিক ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী বেতন-ভাতার অঙ্গীকার করবেন শুধু তারাই প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি পাবেন। বেতন-ভাতা অনিয়মিত হলে বা পরপর তিন মাস বা ছয় মাস না দিলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও নির্ধারণ করে দেওয়া। প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে পরিশোধিত মূলধন থেকে কর্মীদের পাওনা মেটাতে হবে। আরও বলি, সেন্সরশিপ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থার স্থায়ী অবসান প্রয়োজন। সাংবাদিকদের দেখতে হবে, জাতীয় প্রেস ক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ডিআরইউসহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমিতি যেন পেশার সম্মান বজায় রেখে চলতে পারে। সংস্কার এসবেও দরকার। সংবাদপত্রের মালিকানা ওয়েজবোর্ড বিটিভিকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বলা হতো সাহেব-বিবির বাক্স। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এর স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি আর এগোয়নি। ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আকাশ-সংস্কৃতি অর্থাৎ স্যাটেলাইট টিভির সূচনা ঘটে। এক হিসাবে বর্তমানে দেশে টিভি ৪৫টি, ২৮টি এফএম, ৩২টি কমিউনিটি রেডিও, ১০০টি অনলাইন পোর্টাল এবং প্রায় ১ হাজর ৩০০ পত্রিকা রয়েছে। শেখ হাসিনা অধিকাংশ গণমাধ্যমের লাইসেন্সদাতা এবং তিনি গর্ব করে বলতেন, এসবের লাইসেন্স তো আমিই দিয়েছি। এসবের অধিকাংশ মালিক সমাজের লুটেরা শ্রেণি এবং আওয়ামী লীগের নেতা বা সমর্থক। এক জরিপে দেখা যায়, ৩২টি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এসবের মালিক। তারা নির্লজ্জভাবে সরকারকে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি জনগণকে সত্য জানতে দেয়নি। আর নিজস্ব ব্যবসায়িক ধান্দা ও প্রতিযোগীকে ঠেলাঠেলির জন্য গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। ধনী পরিবারের বৈশিষ্ট্য যেমন নানা শিল্পের মালিক, তেমনি মিডিয়ার মালিকানাও তাদের হাউসে থাকতে হবে। শেয়ারবাজার বা ভূমিবাজারে দস্যুতা করে শত শত কোটি টাকা কামিয়ে মিডিয়ায় সামান্য খয়রাতি করলেই তো চলে। অন্যদিকে কতিপয় সাংবাদিক নেতাকে স্বৈরাচারী সরকার টিভি, পত্রিকার লাইসেন্স এবং পুঁজি দিয়েছে। কালো টাকার অবাধ লগ্নি ঘটেছে মিডিয়ায়। সাংবাদিকরা তাদের জন্মদিন পালন করতেন অভিজাত হোটেলে। তারা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির সদস্য ছিলেন। কমিশনের পক্ষ থেকে সংবাদপত্র শিল্পের পুঁজি মালিকদের মিডিয়া-মনস্কতা, সাংবাদিক-কর্মচারীদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি দেখা উচিত। সাংবাদিক-কর্মচারীদের ওয়েজবোর্ড নিয়ে কারও কারও আপত্তি আছে। কিন্তু ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় সাংবাদিকরা মজুর। নতুন সমাজ বাস্তবতায় আমরা শ্রমিক পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করি। কিন্তু শ্রমিকের অধিকার আইনে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। তা ছাড়া টিভি ও পত্রিকার সাংবাদিকদের বেতনবৈষম্য দূর করাও জরুরি। সাংবাদিক সমাজ সাংবাদিকের সংখ্যা এখন প্রচুর। কিন্তু মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে চরম রাজনীতিকরণের কারণে সামাজিক মর্যাদা আগের মতো নেই। সাংবাদিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো যাচাই প্রক্রিয়া নেই। তাই মিডিয়া লিটারেসির প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের মিডিয়া সে কারণে ন্যাশনাল মিডিয়াও হয়ে উঠতে পারেনি। বড় বড় রাজনৈতিক দল মিডিয়াকে কবজা করতে ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী এগিয়ে। তাই দলীয় কর্মীও ঢুকছে সাংবাদিক পরিচয়ে। ঢাকার দুটি সাংবাদিক ইউনিয়নে সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি। বিশ্বাস হয় ঢাকায় এত লোক সাংবাদিকতা করে? ফুটপাতের বা সেলুনের নাপিতও রয়েছে সদস্য হিসেবে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যবিদ্যা পড়া তরুণরা আসছে। আমাদের পূর্বসূরিরা যেমন গদ্য, পদ্য লেখালেখির মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় এসেছেন, সে ঐতিহ্য আর নেই। এসব বলার একটাই কারণ। যে গণঅভ্যুত্থান স্বপ্ন দেখিয়েছে নতুন বাংলাদেশের, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সংবাদপত্রকেও তার উপযোগী করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল এবং প্রেস ইনস্টিটিউটকে আরও ক্ষমতাবান ও সক্রিয় হতে হবে। প্রেস কাউন্সিলের কার্যপরিধির মধ্যে সংবাদপত্রের জন্য আচরণবিধি তৈরি, সংবাদপত্রের জন্য উচ্চ আদর্শসম্পন্ন আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, সাংবাদিকদের জন্য জনরুচির উচ্চমান রক্ষা করা, সাংবাদিকদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং জনসেবায় কাজ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি প্রমুখ। তারপর মানহানির বিচারও করতে পারে। তবে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে আপিল বিভাগের বিচারক বসানোর বিধান পরিবর্তন করে একজন সিনিয়র সাংবাদিককে পদায়ন করা বাঞ্ছনীয়। তদুপরি জুডিশিয়াল কমিটির সদস্য হিসেবে চলমান সরকার সমর্থকদের নিয়োগ দিলে ন্যায়বিচারও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। প্রেস ইনস্টিটিউটের উচিত, যারা সাংবাদিকতার আছে ও আসতে চান, এমনদের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা। সরকারি মালিকানাধীন সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনা। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার পুঁজি সরকারের হাতে কিছু রেখে বাকিটা সংবাদপত্র সম্পর্কিত মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, যাতে সংস্থাটির সাংবাদিকতা ও জবাবদিহি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে বলব, রাষ্ট্র পরিচালকরা যদি সহিষ্ণু, উদার গণতান্ত্রিক হন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হন, তবেই মিডিয়া সংস্কার সফল হবে। লেখক: সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব